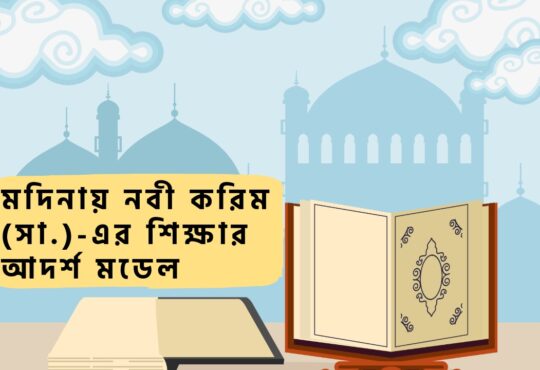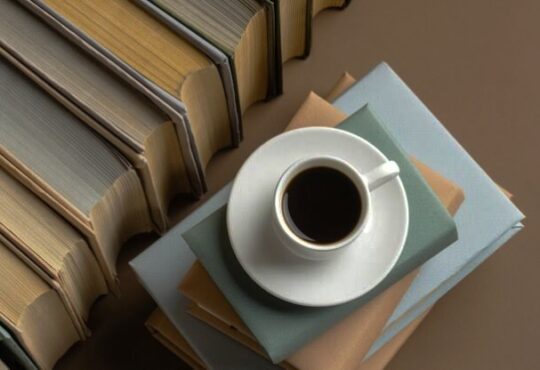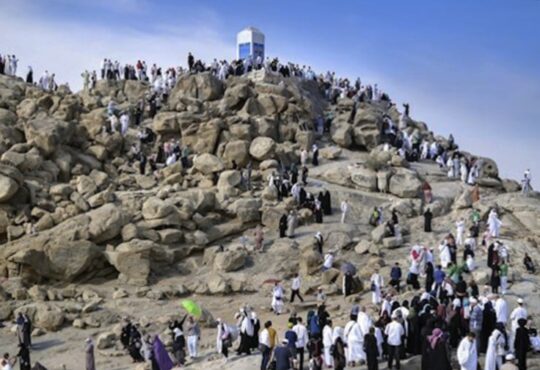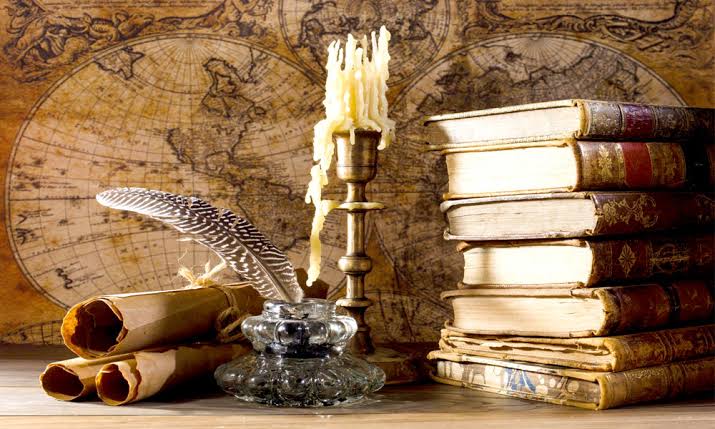
লেখক: সেখ আনিসুর
তিনি হলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কথিত আছে, তাঁকে সৃষ্টি না করা হলে এই বিশ্ব-ভুবন সৃষ্টি হতো না। বিশ্ব-জমিনের উপর প্রবাহিত জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক উস্কানি কিংবা হানাহানি এবং অরাজকতার এই দাবদাহের মাঝে তিনিই প্রথম বলেছিলেন: “আরবের উপর অনারবের কোন প্রাধান্য নেই, কিংবা অনারবের উপর আরবেরও কোন প্রাধান্য নেই।” যেখানে ধনীর সঙ্গে গরিবের ভেদাভেদ, নেতার সঙ্গে কর্মীর ভেদাভেদ, রাজার সঙ্গে প্রজার ভেদাভেদ – এহেন বিচ্ছিন্নতার মাঝেও তিনি মানবতাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর ছায়াতলে এক সারিতে দাঁড় করিয়েছিলেন।
বর্তমান যুগের ইঁদুর দৌড়ের এই ক্লান্তিকর যাত্রাপথে, মানুষ যখন তার মানবিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন তিনিই আবার শিখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে জাগিয়ে তুলতে হয় মানবতার প্রদীপ। তিনি আলো পৌঁছে দিয়েছিলেন অন্ধকারের গোপন কুঠুরিতে। অন্ধকার থেকে বার করে এনেছিলেন মানুষকে এক উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। তিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন, অনন্তকালের যাত্রাপথে কিভাবে পাড়ি দিতে হয়, কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়। তিনি মানুষকে শিখিয়েছিলে – শ্রেষ্ঠত্ব কোন একক বিষয় নয়; বরং সকলের কণ্ঠে একই লগ্নে যখন আল্লাহর মহিমা উচ্চারিত হবে, তখনই মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সিরাজুম মুনিরা, এমন প্রদীপ, যা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বভুবনকে আলোকিত করতে থাকবে।
নিজ দেশ ত্যাগ করে তিনি যখন মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, মদিনার আপামর জনসাধারণ তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে গান ধরলো:
“তলা‘আল বাদরু ‘আলাইনা।”
তিনি পবিত্র মদিনার ফুলের মতো সুন্দর বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন:“তোমরা কি আমায় ভালোবাসো?”
বাচ্চারা বলল: “হ্যাঁ।”
তিনি বললেন: “আমিও তোমাদের ভালোবাসি।”
তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার নামের অর্থই হলো চরম প্রশংসিত। প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁর আদর্শকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের থেকেই নয়; বরং এই সমগ্র বিশ্বভূমণ্ডলে অবস্থিত প্রতিটি বালুকণা, সাগর-নদী, পাহাড় এবং সংবেদনশীল প্রতিটি অস্তিত্ব থেকেও তিনি প্রশংসিত। আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করছেন যে, তিনি এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অর্থাৎ এই ভালোবাসা, এই প্রশংসা কিংবা সম্মান শুধুমাত্র এই জমিনের বুকে জীবিত থাকা মানুষদের পক্ষ থেকে নয়; বরং দৃশ্য-অদৃশ্য প্রত্যেক পরিসর থেকেই তাঁর প্রশংসা এবং তাঁর গুণগান অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। আর এই প্রেমধারাই যে নিজেকে সামিল করে নিতে পারে, সেও হয়ে ওঠে ধন্য। বলা চলে তার জীবন হয়ে ওঠে সার্থক। বাংলা সাহিত্যের একাধিক কবি-সাহিত্যিক নিজেদেরকে নবী প্রেমের ফাল্গু ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। নবী প্রেমের বসন্তে অনেকেই হয়ে উঠেছিলেন আশেকে রাসুল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবেসে দিওয়ানা হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের অনেকেই।
এই সাধক-রূপী সাহিত্যিকদের বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে আমরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে উঠতে পারিনি, কিংবা তাদের পরিচয় আজ হয়তো লুপ্ত হয়েছে আমাদের হৃদয়ের অন্দরমহল থেকে। তবুও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি, দেখতে পাই সেই নক্ষত্রদের, যারা তাদের কবিতার চরণে বর্ণিত করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপার মহিমাকে। পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন নবী প্রেমের মনিমালা।
সাহিত্যের উৎপত্তি মাটি থেকে। মাটির উপর মানুষের বসবাস, আর এই মানুষের বাঙ্ময়যুক্ত ভাষার প্রকাশই হলো সাহিত্য। বাংলা ভাষা তার হাজার বছরের যাত্রাপথ অতিক্রম করেছে। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো চর্যাপদ। ‘কা আ তরু বর…’ থেকে উৎপত্তি ঘটা বাংলা সাহিত্যের যে নদী প্রবাহিত হয়েছে, বর্তমানে তার কূলকিনারা কোথায় যে গিয়ে ঠেকেছে, তা আন্দাজ করতে পারা বড়ই কঠিন। ভাষা বড়ই ছোঁয়াচে, লোকোমুখে ছড়িয়ে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি।
আদতে বাংলা ভাষার সীমানা কতটুকু, তা নির্ধারণ করা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে একটু খাটুনিরই বটে। এই বিষয়ে ড. নিহার রঞ্জন রায় বলেন, “হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান যুগে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা বারবার পরিবর্তিত হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমারূপ এই বিশাল ভূখণ্ডটি এই ভাবেই নির্ধারিত হতে পারে: উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হতে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য; উত্তর-পূর্ব দিক ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারভঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্ব দিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগনা, ছোট নাগপুর, মালভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর, ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।”
এ তো গেল বাংলা ভাষার সীমানা। কিন্তু এই ভাষা এবং এই ভাষায় রচিত সাহিত্যের যে ধারাবাহিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কেও একটু জেনে রাখা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার কালবিন্যাস করতে গিয়ে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বাংলা ভাষার উৎপত্তি অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার মতোই নদীপ্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নদীপ্রবাহের মতোই এ ভাষা কালানুক্রমিকভাবে যত অগ্রসর হয়েছে, ততই এর পরিবর্তন হয়েছে, ততই এর আকার-আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর এই বিংশ শতাব্দীতে এ ভাষা সহস্রমুখী হয়ে চলেছে নব নব সম্ভাবনার সাগরসঙ্গমে। এদেশে আর্যাভিযানের পূর্বে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ জাতি বাস করত। কালক্রমে এ দেশে আর্যসংস্কার দৃঢ়মূল হল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষাও এদেশে প্রচলিত হল এবং সংস্কৃত, প্রাকৃt, অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে বাংলা ভাষা ভূমিষ্ঠ হল। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বয়ে চলেছে। এ ভাষার বয়স অন্যূন হাজার বছর। ভাষাগত পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে বাংলা ভাষাকে যথাক্রমে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। আদিযুগের বাংলা ভাষা বা প্রাচীন বাংলা ভাষার সীমা খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। চর্যা-চর্যাবিনিশ্চয়ে এ ভাষার প্রাথমিক দৃষ্টান্ত মিলবে। এরপর মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কাল, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এর বিস্তার। খ্রিস্টীয় ষোড়শ থেকে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০) পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার অন্ত্যপর্যায় বিস্তৃত। এ স্তরে বাংলা ভাষার রূপান্তর প্রায় আধুনিক কালের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ও পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্যের প্রভাবে প্রচুর তৎসম (অর্থাৎ সংস্কৃত) শব্দপ্রয়োগ হতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শব্দের ব্যবহারে বাঙালি হিন্দু বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে।”
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যে নিদর্শনগুলি পাওয়া যায়, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় – কোনো মুসলিম কবি নয়, বরং অমুসলিম সাহিত্যিকের রচনাতেই প্রথম দেখা মেলে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণগান। এ থেকে বোঝা যায়, সাহিত্যের রূপ-রস-গন্ধে ভালোবাসাটাই প্রধান, ভক্তিটাই আসল।
ড. এস. এম. লুৎফুর রহমান এ তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে লিখেছেন, “আনুমানিক নয়, নিশ্চিত রূপেই ১০০০ থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিত রচিত কলিমা জাল্লাল নামক রচনায় পহেলা রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তারিফ করা হয়েছে। তাঁকে অমুসলিমদের ইলাহ (প্রভু বা উপাস্য) ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করে গৌড়ে মুসলিম বিজয় অভিযানকে বেহেশতি রহমত রূপে বয়ান করতে বলা হয়েছে,
“ব্রহ্মা হৈল মুহাম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম্ব হৈলা মূল পানি।
গণেশ হৈলা গাজী, কার্ত্তিকা হৈলা কাজী,
ফকীর হৈলা যথ মুনি।”
মধ্যযুগে বাংলায় স্থাপিত হয় মুসলিমদের সাম্রাজ্য। সে সময় মুসলিম শাসকদের তত্ত্বাবধানে বাংলা সাহিত্য ফুলে–ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের নদী প্রবাহিত হতে থাকে উত্তর থেকে দক্ষিণ, কিংবা পূর্ব থেকে পশ্চিমে। বাংলার রাজসিংহাসনে একই নামধারী তিনজন সুলতান শাসন করেছেন – গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ, গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ এবং শুধুই গিয়াস উদ্দিন। এদের ছাড়াও গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ কিছুকাল রাজত্ব করেছেন। এই শাসকের রাজত্বকালে প্রভাতের সূর্যের মতো আবির্ভাব ঘটে মোহাম্মদ সাগীর-এর। তিনি রচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম রোমান্টিক কাব্য ‘ইউসুফ জুলেখা’। কথিত আছে, ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর পুস্তক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ধর্মীয় নীতি–শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এ কাব্য রচনা করেছিলেন। এ কাব্যের ভূমিকায় তিনি মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন। কাব্যের শুরুতে তিনি মহানবীর নামে লিখেছিলেন:
“জীবাত্মার পরমাত্মা মুহাম্মদ নাম,
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম।
যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন,
মুহাম্মদ হোন্তে কৈলা তা সব রতন।
একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবীকূল,
মুহাম্মদ তান মধ্যে প্রধান আদ্যমূল।”
মুসলিম শাসনামলের আরও এক প্রাচীন কবি জৈনুদ্দীন ছিলেন বাংলার সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি। তাঁর “রাছূল বিজয়” কাব্যে অসাধারণ রণকুশলী হিসেবে নবীর প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে:
“নিঃসরিলা নবীবর সঙ্গে অশ্ববার,
প্রচণ্ড মৃগেন্দ যেন সাতাইশ হাজার।
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল,
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল।”
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মুসলিম কবি ছিলেন আলাওল ও দৌলত কাজী। দৌলত কাজী নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু তথ্য তাঁর পাঠকের সামনে না তুললেও আলাওল তাঁর জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে অনেক তথ্যই আমাদের দিয়ে গেছেন। সূফী ঘরানার এই বিদগ্ধ কবির বিখ্যাত কাব্য হলো ‘পদ্মাবতী’। রাজস্থানের চিতোরের রানী পদ্মাবতী ও আলাউদ্দিন খিলজির প্রেমকাহিনী সে সে অঞ্চলের অলিতে-গলিতে বহুল আলোচিত ছিল। সেই কাহিনীই তিনি কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন পদ্মাবতী-তে। তবে শুধু প্রেমকাহিনী নয়, তাঁর লেখনীর মাঝে ধরা পড়েছে নবীপ্রেমের চরণও:
“পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার,
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার।
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা,
সেই জ্যোতিমূলে ত্রিভুবন নিরমিলা।”
অন্যদিকে দৌলত কাজী তাঁর কবিতায় নবী বন্দনা প্রকাশ করে লিখেছিলেন:
“মহাম্মদ আল্লাহর রসূল সখাবর,
যার নূরে ত্রিভূবন করিছে প্রসর।”
শুধু পুরুষ কবিরাই নন, মধ্যযুগে বহু নারী সাহিত্যিক-এরও দেখা মেলে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। মধ্যযুগের অন্যতম নারী কবি তিনি। তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘রূপজালাল’-এর শুরুতেই ফুটে উঠেছে অভূতপূর্ব নবী বন্দনা–
“প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন,
যাঁহার সৃজন হয় এ তিন ভুবন।
তৎপর বন্দনা করি নবীর চরণ,
যাঁহার প্রভাবে হয় অন্তিম তরণ।”
এছাড়াও পরবর্তীকালে শেষ চান্দ, সৈয়দ হামজা, মুনশী জান, শাহ্ গরীবুল্লাহ্, মুহাম্মদ দানেশ, খাতের মুহাম্মদ প্রমুখ কবিরা তাঁদের কাব্যে নানাভাবে ও নানাভঙ্গিতে নবীবন্দনা উপস্থাপন করেছেন। এযুগের সাহিত্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, ফারসি রচনার প্রভাব। বিশেষভাবে ওমর খৈয়ামের মরমী টান, মধ্যযুগের বহু কবি তার লেখাতে যত্ন সহকারে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এঁরা সকলে মধ্যযুগের কবি। তাঁদের সময়কাল আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত।
আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, যার নাম বিশেষভাবে নিতেই হয় তিনি হলেন মীর মশাররফ হোসেন। কারবালার করুণ দৃশ্যকে তিনি বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসে যেভাবে ব্যক্ত করে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন, তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা হয়ে উঠেছিল আকাশচুম্বী। তিনি তাঁর ‘মৌলুদ শরিফে’ নবীপ্রেমেr জজবাতে লিখেছিলেন:
“তুমি যে সত্য পয়গম্বর
সে প্রমাণ আছে বহুতর
তবু যার মানতে ধোঁকা
সে তার করমের (কর্মের) লেখা।”
তবে ভক্তির অতল স্রোতে তলিয়ে না গিয়ে, যথার্থ নবী সাঃ-এর জীবনীকে কাব্যরসে ফুটিয়ে তুলতে যদি কেউ স্বার্থক হন, তিনি হলেন কবি ফররুখ আহমেদ। তাঁর রচিত ‘সিরাজাম মুনিরা’ সর্বজনবিদিত। কাজী নজরুল ইসলামও নবীপ্রেমে রচনা করেছিলেন ‘মরুভাস্বর’ শীর্ষক একখানা কাব্যগ্রন্থ, যা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ বলা চলে।
তবে নবী বন্দনায় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নজরুল যে ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন, তাকে অতিক্রম করার সাধ্যি আজ পর্যন্ত কারোর হয়নি। তাঁর ‘ফাতেহা-ই দোয়াজদহম’ নবীবন্দনায় লিখিত শ্রেষ্ঠতম কবিতা। লেটো দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গ্রামীণ বাংলার আধ্যাত্মিক রসকে তিনি যেভাবে আস্বাদন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন, তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নজরুল রচিত নবী প্রেমের কবিতাগুলিতে।
হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে তিনি বর্ণনা করে বলেছিলেন:
“আমি যদি আরব হতাম ওই মদিনার পথ
সেই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হযরত।”
মানুষ যখন ভালোবাসায় সমস্ত পিছুটানকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, তখন সে ভালোবাসার পাত্রের প্রতি শুধু নিজেকেই নয়, প্রকৃতিকেও উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাইতো তিনি লিখেছিলেন:
“মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কিরে তোর কণ্ঠেরই গান এতই মধুর লাগে।”
বাৎসল্য রসে ভরপুর তাঁর যে রচনাখানি আজও পাঠকের হৃদয় প্রেমের সঞ্চার ঘটায় তা হলো:
“তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে,
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে,
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।
তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।”
শুধু ভাব নয়, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া আদর্শকে জমিনে বাস্তবায়নের সদিচ্ছাও ছিল নজরুলের। মুসলিম জাহান যখন এহেন উচ্চ আদর্শকে ভুলতে বসেছে, তখন তিনি নবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখলেন:
“তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ,
ক্ষমা করো হজরত।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ,
তোমার দেখানো পথ–
ক্ষমা করো হজরত।”
নবী বন্দনায় যারা নিজেদেরকে বাংলা সাহিত্যের জমিনে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম এবং নজরুলের পরেই যাকে রাখতে হয় তিনি হলেন গোলাম মোস্তফা। তাঁর রচিত গান আজও গ্রাম বাংলার প্রতিটি নবীপ্রেমিকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। মাহফিল, মিলাদ কিংবা শীতকালীন জলসায় বাংলার ঘরে-ঘরে তার গান পৌঁছে যায় ওয়াজ কারীর সুরেলা কণ্ঠে।
“তুমি যে নূরেরই নবী, নিখিলের ধ্যানেরই ছবি।”
তাঁর রচিত সংগীতের একখানা চরণ যেন গ্রাম বাংলার নবীপ্রেমের প্রধান উপকরণ।
এছাড়াও মতিউর রহমান মল্লিক, শেখ আব্দুর রহিম সহ বহু সাহিত্যিকের লেখালেখিতে ছড়িয়ে আছে মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর জীবন সুধা।
(লেখকের নিজস্ব অভিমত)