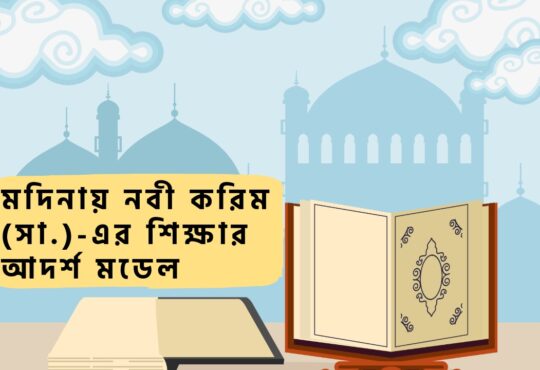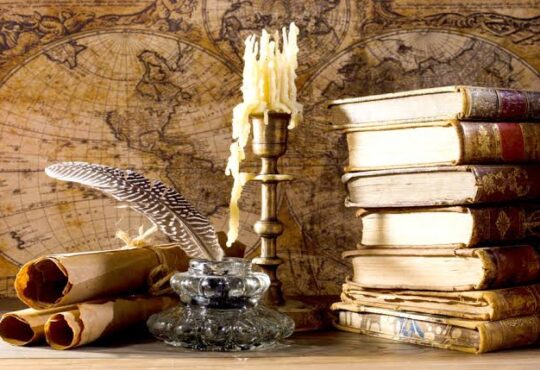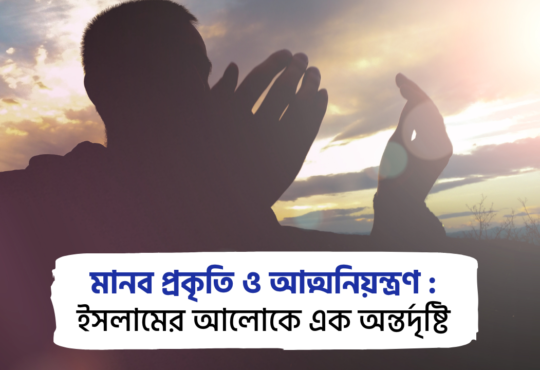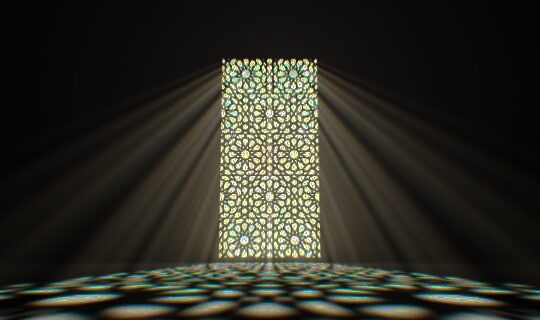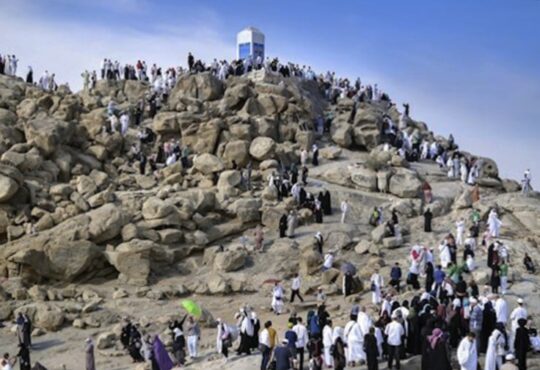ওয়াকফের অর্থ ও সংজ্ঞা
‘ওয়াকফ’ আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ স্থগিত করা, আবদ্ধ করা, স্থির রাখা, নিবত্তৃ রাখা। ওয়াকফ ইসলামি শরিয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা। কোনো সম্পত্তি এর মালিক নিজের মালিকানা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সম্পত্তি ঘোষণা করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জনকল্যাণ বা জনসেবার জন্য উৎসর্গ করলে সেই উৎসর্গ করার
কাজটিকে ওয়াকফ বলা হয়।
ইসলামে ওয়াকফের গুরুত্ব
ইসলামে ওয়াকফের বিধান হচ্ছে এটি একটি নেকীর কাজ ও মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে সহিহ্ হাদিস। হযরত উমার রা. বলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সা. আমি খায়বারে এমন একটি সম্পদ পেয়েছি যে সম্পদের চেয়ে দামি কোনও সম্পদ আমি কখনও পাইনি। আপনি এই সম্পদের বিষয়ে আমাকে কী নির্দেশ দেন?’ তিনি বলেন, ‘যদি আপনি মূল সম্পত্তিকে আবদ্ধ করে (ওয়াকফ করে) সদকা করে দিন। কিন্তু মূলটা বিক্রি করা যাবে না, হেবা করা যাবে না এবং মিরাস হিসেবে মালিক হওয়া যাবে না।’
তখন হযরত উমার রা. এই সম্পদ গরিব-মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তা, পথিক ও মেহমানের জন্য সদকা করে দেন। (সহিহ্ বুখারী ও সহিহ মুসলিম, বুখারী, হাদিস: ২৫৮৬)
ফলে হযরত উমার রা. উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য সদকা করে দেন। সহিহ্ মুসলিমে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোনও বনী আদম মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায়; কেবল তিনটি আমল ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া কিংবা এমন ইলম; যে ইলম দিয়ে তার মৃত্যুর পরেও উপকৃত হওয়া যায় কিংবা নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (সহীহ মুসলিম- ১৬৩১)
জাবের (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সপাহাবীদের মধ্যে যারই সক্ষমতা ছিল, তিনি ওয়াকফ করে গেছেন।’ কুরতুবী বলেন, ‘বিশেষত, সেতু ও মসজিদ ওয়াকফ করার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোনও মতভেদ নেই; অন্য ক্ষেত্রে মতভেদ আছে।’ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ওয়াকফের উদাহরণ হচ্ছে ‘মসজিদে কোবা’। ৬২২ সালে মদিনায় নির্মিত হয়। তারও ছয় মাস পর ইসলামি ওয়াকফের দ্বিতীয় উদাহরণ মদিনার কেন্দ্রে মসজিদে নববী। রাসূল সা.-এর সময় পেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের আমলে অনেক ওয়াকফ কার্যক্রম চালু হয়। মুসলিম সমাজে বর্তমানে ওয়াকফের ধারণা তেমন পরিচিত নয়। মানুষ এই বিষয়ে কোনও ধারণাই রাখতে চায় না। তবে আমাদের চেষ্টা চেষ্টা ছাড়া আর কী বা করার আছে। দেশে ওয়াকফের প্রতি মানুষকে উৎসাহ দেওয়া ও তার সাওয়াবের বিষয়ে আলাপ করা আবশ্যক।
ওয়াকফের প্রকারভেদ
ওয়াকফ তিন ধরনের। যেথা— ১. ওয়াকফ লিল্লাহ অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফ। ২. ওয়াকফ আলাল আওলাদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ওয়কফ। ৩. মিশ্র ওয়াকফ। শুধু ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ওয়াকফকে ওয়াকফ ফি লিল্লাহ বলা হয়। উৎসর্গকারীর নিজের জন্য বা পরিবার বা বংশধরদের উপকারের জন্য যখন প্রভূতভাবে উৎসর্গ করা হয় তখন তাকে ওয়াকফ আলাল আওলাদ বলা হয়। মিশ্র ওয়াকফে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রকৃতির সর্বজনীন উদ্দেশ্যের পাশাপাশি উৎসর্গকারীর, তাঁর পরিবার ও বংশধরদের ভরণ-পোষণ উভয় উদ্দেশ্যই কাজ করে।
ওয়াকফ-এর শর্ত ও বিধান
ওয়াকফ সহিহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: ১। ওয়াকফকারী লেনদেন করার উপযুক্ত হওয়া; যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
২। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মূলকে অটুট রেখে এর থেকে অব্যাহতভাবে উপকৃত হওয়া যায় এমন হওয়া। যে জিনিসের মূল অটুট থাকে না এমন জিনিস ওয়াকফ করা যায় না; যেমন— খাবার।
৩। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি নির্দিষ্ট হওয়া। তাই কোনও অনির্দিষ্ট সম্পত্তি ওয়াকফ করা সহিহ্ নয়। যেমন— কেউ যদি বলে যে, আমি আমার কোনও একটি দাসকে কিংবা আমার কোনও একটি বাড়িকে ওয়াকফ করলাম।
৪। ওয়াকফ নেকীর কাজে হতে হবে; যেমন— মসজিদ, সেতু, মিসকীন, পানির উৎস, ইলমী কিতাবপত্র, আত্মীয়স্বজন। কেননা, ওয়াকফ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ নৈকট্য হাছিল। নেকী নয় এমন খাতে ওয়াকফ করা সহিহ নয়। যেমন— অবিশ্বাসীদের উপাসনালয়ের জন্য ওয়াকফ করা, নাস্তিক্যবাদী পুস্তকের জন্য ওয়াকফ করা, মাজারে বাতি জ্বালানো কিংবা সুগন্ধি দেওয়ার জন্য ওয়াকফ করা কিংবা মাজারের রক্ষকদের জন্য ওয়াকফ করা। কেননা, এগুলো হচ্ছে গুনাহের কাজ, শিরক ও কুফরের কাজে সহযোগিতা করা।
৫। নির্দিষ্ট কারো জন্য ওয়াকফ করলে সে ওয়াকফ সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ওই ওয়াকফ সম্পত্তির উপর সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেহেতু কারও জন্য ওয়াকফ করা মানে তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। তাই যে ব্যক্তি মালিক হতে পারে না তার জন্য ওয়াকফ করা সহিহ নয়; যেমন-— মৃতব্যক্তি বা পশু।
৬। ওয়াকফ সহিহ হওয়ার জন্য অবিলম্বে কার্যকরযোগ্য হওয়া শর্ত। তাই নির্দিষ্ট সময়কেন্দ্রিক ওয়াকফ কিংবা বিশেষ কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ওয়াকফ করা সহিহ নয়। তবে কেউ যদি তার মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াকফ করে তাহলে সহিহ হবে। যেমন কেউ বলল যে, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার ঘরটি গরিবদের জন্য ওয়াকফ। যেহেতু আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, ‘হযরত উমার রা. ওসিয়ত করে গেছেন যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে ‘সামগ’ (তার একটি জমি) সদকা।’ এই বিষয় সবাই জেনেছে। কিন্তু কেউ এর বিরোধিতা করেননি। সুতরাং এটি ইজমা (সর্বসম্মত অবিমত)। মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত ওয়াকফ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে করা যাবে। কারণ তা ওসিয়তের পর্যায়ভুক্ত। ওয়াকফকারীর মধ্যে কতিপয় শর্ত থাকতে হবে, নতুবা তার ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। শর্তগুলো হচ্ছে—
১. ওয়াকফকারী দান করার যোগ্য হতে হবে। অতএব, জবরদখলকারী ও যার মালিকানা এখনও স্থির হয়নি এমন লোকদের পক্ষ থেকে ওয়াকফ করা জায়েয হবে না।
২. ওয়াকফকারী বিবেকবান (জ্ঞানসম্পন্ন) হতে হবে। অতএব, পাগল ও বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না।
৩. বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অতএব, শিশুর ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না, চাই সে ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী হোক বা না হোক।
৪. বুদ্ধিমান হওয়া। অতএব, নির্বোধ লোকের ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না।
৫. ওয়াকফকৃত বস্তুতে অন্যের অধিকার সম্পৃক্ত না থাকা।
৬. ওয়াকফকৃত বস্তু দ্বারা ‘উরফ তথা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উপকার গ্রহণে সক্ষম হওয়া।
৭. ওয়াকফকৃত বস্তুতে বৈধ উপকার থাকা।
ওয়াকফ ও অসিয়তের মধ্যে পার্থক্য
‘ওয়াকফ’ হল মূল স্বত্ব নিজের রেখে বস্তুর উপকার দান করা। অন্যদিকে অসিয়ত হল দানের মাধ্যমে মৃত্যুর পরে বস্তুগত বা অবস্তুগত (উপকার) জিনিসের মালিক বানানো। বেশিরিভাগ আলেমের মতে, ওয়াকফ করলে তথা বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে এবং ওয়াকফ ফেরত নেওয়া যায় না। কেননা রাসূল সা. হযরত উমার রা.-কে বলেছেন ‘তুমি ইচ্ছে করলে জমির মূল স্বত্ব ওয়াকফে আবদ্ধ রেখে উৎপন্ন বস্তু সদকা করতে পার।’
(বুখারী, হাদিস: ২৫৮৬)
অন্যদিকে অসিয়ত করলে বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যকীয় হলেও অসিয়তকারী তার অসিয়তের পুরোটাই বা আংশিক ফেরত নিতে পারবে।
ভারতবর্ষে ওয়াকফের ইতিহাস ও বিভিন্ন বিল
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু লোকসভায় বিলটি পেশ করেন। ইসলামি শাসনের আবির্ভাবের সাথে সাথে ভারতে ওয়াকফের ধারণা চালু হয়। সেই সময়কালে, ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা খুবই তাত্ত্বিকভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। ভারতে ওয়াকফের ধারণাটি দিল্লি সালতানাতের সময়কার যখন সুলতান মুইজদ্দিন সাম ঘোর মুলতানের জামে মসজিদের পক্ষে দুটি গ্রাম উৎসর্গ করেছিলেন এবং এর প্রশাসন শাইখুল ইসলামের বিকাশে হস্তান্তর করেছিলেন। ইসলামি শাসনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা বদ্ধিৃ পায়।
সেই সময়কালে, ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামি বৃত্তি ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে, ওয়াকফ ধর্মান্তরকরণ এবং ধর্মীয় পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সুবিধার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। টমাস আর্নল্ড তার ‘দ্য প্রিচিং অফ ইসলাম: এ হিস্ট্রি অফ দ্য প্রোপাগেশন অফ দ্য মুসলিম ফেইথ’ বইয়ে অমুসলিমদের মধ্যে ‘সুফিদের’ ইসলামিক ‘মিশনারী’ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ইতিহাসবিদ মুজাফফর আলম তার ‘দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পলিটিক্যাল ইসলাম: ইন্ডিয়া ১২০০- ১৮০০’ বইতেও উল্লেখ করেছেন যে সুফিরা হিন্দুদের ইসলামে দীক্ষিত করতেন। রিচার্ড ইটন তার রচনায়, ভারতে ইসলামে ধর্মান্তরের অধ্যয়নের পদ্ধতি’ এই প্রক্রিয়াটিকে ‘অ্যাক্রিশন অ্যান্ড রিফর্ম’ বলে অবিহিত করেছেন, যার মাধ্যমে সুফি সাধকরা হিন্দু/স্থানীয় রীতিনীতির উপযুক্ত হবেন এবং নাম মাত্রভাবে জনসংখ্যাকে ইসলামে রূপান্তর করবেন।
ব্রিটিশ আমলে ওয়াকফ প্রারম্ভিক দিনগুলিতে, ব্রিটিশ ভারত হিন্দু ও মুসলিম দানপত্রে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত ছিল। ১৮১০ সালের বেঙ্গল কোড রেগুলেশন প্রথম প্রবিধানটির লক্ষ্য ছিল মসজিদ, মন্দির এবং
পাবলিক বিল্ডিংগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাড়া এবং উৎপাদন পরিচালনা করা। একইভাবে, মাদ্রাজ কোড রেগুলেশন ১৮১৭ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জন্য একই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই প্রবিধানগুলি ব্রিটিশ সরকারকে ধর্মীয় ট্রাস্টগুলির তত্ত্বাবধান করতে এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার অনুমতি দেয়।
১৮৩৯ সাল নাগাদ, খ্রিস্টান মিশনারিদের আপত্তি ব্রিটিশদের তাদের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে পরিচালিত করে যার ফলে মন্দির ও মসজিদের তহবিল অব্যবস্থাপনা এবং আত্মসাৎ হয়। তৎকালীন সরকার ১৮৬৩ সালের ধর্মীয় এনডাউমেন্টস অ্যাক্ট প্রণয়ন করে যা সরকারকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেয় এবং প্রয়োজনে দালতের হস্তক্ষেপে স্থানীয় কমিটি দ্বারা ব্যবস্থাপনা চালু করে।
১৮৯০ সালের চ্যারিটেবল এনডাউমেন্টস অ্যাক্ট আরও দাতব্য সম্পত্তির জন্য কোষাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২০ সালে, চ্যারিটেবল অ্যান্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট অ্যাক্ট যে-কোনও আগ্রহী ব্যক্তিকে ট্রাস্টের বিচারিক তদারকি করার অনুমতি দেয়, আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
১৮৯৪ সালে, আবদুল ফাতা মুহাম্মদ ইসহাক বনাম রুসোময় ধুর মামলায় একটি রায় আসে যা এই বিষয়ে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে। এটি রায় দেয় যে প্রাথমিকভাবে পরিবারের উপকার করা অবৈধ ছিল যদি না সেগুলি দাতব্যের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। রায়ের প্রতি অসন্তোষ ১৯১৩ সালের মুসলিম ওয়াকফ বৈধকরণ আইনের দিকে পরিচালিত করে যা এটিকে উল্টে দেয়।
১৯২৩ সালের মুসলিম ওয়াকফ আইন যথাযথ হিসাব-নিকাশ বাধ্যতামূলক করেছিল, কিন্তু অব্যবস্থাপনা অব্যাহত ছিল। আরও, বেঙ্গল ওয়াকফ অ্যাক্ট (১৯৩৪) এবং বিহার ওয়াকফ অ্যাক্টের মতো সংশোধনীগুলি চালু করা হয়েছিল। এই আইনগুলি প্রমাণ করে যে মুসলিম এনডাউমেন্ট পরিচালনার জন্য নিবেদিত আইনের প্রয়োজন ছিল যা পূর্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ আইনের বিপরীতে ছিল।
স্বাধীনতা-পরবর্তী এবং দেশভাগের পর
১৯৪৭ সালের পর, ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য ১৯২৩ সালের মুসলিম ওয়াকফ আইন প্রযোজ্য ছিল। যাইহোক, ১৯৫৪ সালে, তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ওয়াকফ আইন, ১৯৫৪ প্রবর্তন করেছিল, যা এই সম্পত্তিগুলির প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করেছিল। এটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার সাথে ওয়াকফ বোর্ডও প্রতিষ্ঠা করেছে। যাই হোক, এটি সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ উত্পাদন করেছে, বিশেষ করে একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার বিষয়ে। এই আইনটি স্বাধীনতা-পূর্ববেশ কিছু আইন বাতিলের দিকে পরিচালিত করে এবং ওয়াকফ সম্পত্তির প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করে।
১৯৮৪ সালে, ওয়াকফ তদন্ত কমিটি ওয়াকফ (সংশোধন) আইনের দিকে পরিচালিত একটি প্রতিবেদন পেশ করে যার লক্ষ্য ছিল ওয়াকফ প্রশাসনের পুনর্গঠন এবং আর্থিক ও অপারেশনাল ত্রুটিগুলি সমাধান করা। যাইহোক, মুসলিম সম্প্রদায় এতে তীব্র আপত্তি জানায়, বিশেষ করে ওয়াকফ কমিশনারকে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং আইনটি পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি।
পরবর্তীতে, ওয়াকফ আইন ১৯৯৫ প্রণীত হয়েছিল যা পূর্ববর্তী আইনগুলিকে একত্রিত ও সংশোধন করেছিল। এটি ১৯৮৪ সংশোধনী আইনের প্রধান বিধানগুলিকে ধরে রেখেছে। যাই হোক, মুসলিম সম্প্রদায় এখনও এর বিরুদ্ধে ছিল যার ফলে উন্নতির সুপারিশ করার জন্য একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়েছিল। জেপিসির সুপারিশের ভিত্তিতে, ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ ওয়াকফকে আরও ক্ষমতা প্রদান করে প্রণীত হয়েছিল। ১৯৫৪, ১৯৯৫ এবং ২০১৩ সালে ওয়াকফ আইনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়।
ওয়াকফের সংজ্ঞা ও পরিধি
বছরের পর বছর ধরে ওয়াকফের সংজ্ঞা ও পরিধি পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, ১৯৫৪ ওয়াকফ আইন ব্যবহারকারী এবং ওয়াকফ-আলাল-আওলাদ দ্বারা ওয়াকফ অন্তর্ভুক্ত করার ধারণাটিকে প্রসারিত করেছিল, সম্পত্তিগুলিকে ওয়াকফ হিসাবে বিবেচনা করার অনুমতি দেয় যদি সেগুলি ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বা পারিবারিক প্রেক্ষাপটে উৎসর্গ করা হয়, এমনকি আনুষ্ঠানিক উৎসর্গে ছাড়াই। যাই হোক, ১৯৯৫ আইনটি সংজ্ঞাটিকে প্রসারিত করেছে যা নিশ্চিত করে যে সম্পত্তিগুলি তাদের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেলেও ওয়াকফ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ থাকবে।
যাই হোক, এটি উল্লেখ্য যে ওয়াকফ সম্পত্তির অধিক স্থায়ীত্ব থাকলেই এটি শ্রেণিবদ্ধ থাকবে। ২০১৩ সালে একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছিল যখন সংশোধনীটি যেকোনও ব্যক্তিকে, শুধু মুসলিম নয়, স্থায়ীভাবে ওয়াকফ হিসাবে সম্পত্তি উৎসর্গ করার অনুমতি দেয়। এটি ওয়াকফ সম্পত্তির সম্ভাব্য পুলকে বিস্তৃত করেছে, এটি অমুসলিমদের অবদানের জন্য উন্মুক্ত করেছে।
ব্যবহারকারী দ্বারা ওয়াকফের পরিচিতি ও পরিবর্ধন
ব্যবহারকারী দ্বারা ওয়াকফের ধারণাটি প্রথম ১৯৫৪ আইনে প্রবর্তিত হয়েছিল। এটি আনুষ্ঠানিক উৎসর্গে ছাড়াই ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সম্পত্তিগুলিকে ওয়াকফ হিসাবে বিবেচনা করার অনুমতি দেয়। এটি কবরস্থান এবং মসজিদের মতো সরকারি সম্পত্তির জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল। ১৯৯৫ সালে ধারণাটি সম্প্রসারিত হয়েছিল যার ফলে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেলেও ওয়াকফ থাকবে। ২০১৩ সালের সংশোধনীগুলি এই মর্যাদা নির্ধারণ এবং প্রয়োগ করার জন্য ওয়াকফ বোর্ডের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করেছে, এই ধরনের সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় করেছে।
বিচার-বিভাগীয় কার্যক্রম এবং ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা
প্রাথমিকভাবে, ১৯৫৪ আইনে, দেওয়ানী আদালতের ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। ১৯৯৫ আইনে, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালগুলি তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য চালু করা হয়েছিল। ২০১২ সালে, ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রসারিত করা হয়েছিল এবং এতে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ-সংক্রান্ত বিরোধ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনায় ট্রাইব্যুনালগুলির ভুমিকাকে একীভূত করে।
জরিপের খরচ
১৯৫৪ সালের আইনে, একটি সম্পত্তি জরিপের খরচ মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব ছিল এবং এটি ওয়াকফ সম্পত্তির আয় দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে, ব্যয়টি রাজ্যের আর্থিক বোঝায় স্থানান্তরিত হয়েছিল।
ওয়াকফ বোর্ডের রচনা
১৯৫৪ সালে, মুসলমানদের জন্য বোর্ডের সদস্যপদ সীমিত ছিল না এবং রাজ্যের আইন প্রণেতা, সংসদ সদস্য এবং মুসলিম আইন, প্রশাসন, অর্থবা আইন বিশেষজ্ঞ সহ বিভিন্ন পটভূমির সদস্যদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, ১৯৯৫ আইনে এবং ২০১২ সংশোধনীর পরে, বোর্ড সদস্যদের মুসলিম সম্প্রদায়ের হতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।
বোর্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি
১৯৫৪ আইনটি বোর্ডকে ওয়াকফের আয় ব্যবস্থাপনা, মুতাওয়াল্লিদের নিয়োগ ও অপসারণ এবং ওয়াকফের প্রকৃতি নির্ধারণের মতো ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে। ১৯৯৫ আইন এই ক্ষমতাগুলিকে আরও উন্নত করেছে এবং বোর্ডকে ওয়াকফ বলে গণ্য হলে অন্যান্য আইনের অধীনে নিবন্ধিত ট্রাস্ট বা সমিতিগুলির সম্পত্তি দাবি করার অনুমতি দিয়েছে। ২০১৩ সালের সংশোধনীগুলি এই ক্ষমতাগুলিকে শক্তিশালী করেছে, বোর্ডকে ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রায় অজেয় করে তুলেছে।
সরকারি কর্মচারীর পদবী
১৯৫৪ সালের আইনে শুধুমাত্র কমিশনার, অডিটর এবং বোর্ড অফিসারদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। ১৯৯৫ আইন এটিকে প্রত্যেক মুতাওয়াল্লি, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং ওয়াকফের পদে অধিষ্ঠিত অন্যান্যদের কাছে প্রসারিত করেছে। যাইহোক, ট্রাস্টি বা ম্যানেজারদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।
এতে আগ্রহী যে-কোনও ব্যক্তি বনাম যে-কোনও ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ ১৯৫৪ আইন ‘এতে আগ্রহী যে-কোনও ব্যক্তিকে’ ওয়াকফ সম্পত্তি বিরোধকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি দেয়, প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের লক্ষ্য করে। ১৯৯৫ আইনটি এই শধগুচ্ছটিকে ধরে রেখেছে। কিন্তু বিরোধগুলিকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কাছে নির্দেশ করে। ২০১৩ সালের সংশোধনীগুলি অমুসলিমদের এক বছরের সীমার বাইরে মামলা দায়ের করতে বাধা দেওয়ার বাক্যাংশটি প্রতিস্থাপন করেছে।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ
১৯৯৫ আইন ওয়াকফ বোর্ডের জন্য একজন পূর্ণ-সময়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ প্রবর্তন করেছিল। সিইওকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তির তদন্ত, হিসাব তত্ত্বাবধান এবং ওয়াকফের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান বজায় রাখার জন্য দায়ী।
ওয়াকফ সম্পত্তির বিচ্ছিন্নতা
১৯৯৫ আইনের অধীনে, ওয়াকফ সম্পত্তি বিচ্ছিন্নকরণ-সংক্রান্ত বিধান ছিল। ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয়, উপহার, বিনিময় বা বন্ধকের জন্য এটির জন্য বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন। ২০১৩ সংশোধনী বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতীত এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাকে শুরুতেই বাতিল করে দিয়েছে। একটি সম্পত্তি ওয়াকফ ঘোষণার পর যে ক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়, তা ওয়াকফ থেকে যায়।
অমুসলিমদের কাছে আইনের পরিধি বাড়ানো
অমুসলিমদের দ্বারা ওয়াকফের উদ্দেশ্যে দান করা সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করার জন্য ওয়াকফ আইনের সুযোগ বাড়ানোর জন্য ১৯৫৪ সালের আইনে একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল। ১৯৯৫ আইনে একটি অনুরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এটি বজায় রাখা যে নির্দিষ্ট ওয়াকফ উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের দ্বারা দান করা সম্পত্তি ওয়াকফ আইনের অধীনে পড়ে।
দখল অপসারণের ক্ষমতা
১৯৫৪ আইনে দখলের সমস্যা সমাধান করা হয়নি। ১৯৯৫ সালের আইনে, সিইওকে দখলদারি অপসারণের জন্য বিবেচনামূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ক্ষমতাগুলি ২০১৩ সালে অধিগ্রহণকারী এর একটি নতুন সংজ্ঞা এবং প্রয়োগের জন্য শক্তিশালী প্রক্রিয়াগুলির সাথে প্রসারিত হয়েছিল।
ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য বিশেষ বিধান
১৯৯৫ আইনে স্থানান্তরিত ওয়াকফ সম্পত্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ১৯৫৪ আইনে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই বিধানগুলি নিশ্চিত করেছে যে স্থানান্তরিত সম্পত্তি হওয়ার আগে ওয়াকফ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ সম্পত্তিগুলি ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকবে, এই নির্দিষ্ট সম্পত্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ওয়াকফ আইনের সুযোগ প্রসারিত করেছে।
২০১৩ ওয়াকফ (সংশোধন) আইনে একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল যে ওয়াকফ আইন অন্যান্য আইনের উপর প্রভাব ফেলবে। এটি ওয়াকফ সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াকফ আইনের প্রাধান্য নিশ্চিত করেছে।
১৯৯৫ আইনটি ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের প্রযোজ্যতাকে স্থাবর ওয়াকফ সম্পত্তির দখলের ক্ষেত্রে বাধা দেয়। এটি নিশ্চিত করে যে এই ধরনের স্যুটগুলি সময়সীমার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অনুসরণ করা যেতে পারে।
ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪-এ প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি
ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪, যা লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল, ওয়াকফ আইনে বেশ কয়েকটি বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি হল অমুসলিমদের অবদান অপসারণ। এটি ওয়াকফ’-এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করে, যা বলে যে এটি কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে ইসলাম পালনকারী ব্যক্তির দ্বারা যে-কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি উৎসর্গ করা।
এটি যোগ করে যে ওয়াকফ-আলাল-আওলাদ (দাতার পরিবারের জন্য একটি দান) সৃষ্টির ফলে দাতার মহিলা উত্তরাধিকারী সহ উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকারের অধিকার অস্বীকার করা হবে না। এই সংশোধনীতে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা এবং এতিমদের ভরণপোষণকে এই ধরনের উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির আয় ব্যবহারে যোগ করা হয়েছে।
সংশোধনীটি কালেক্টরের পদ প্রবর্তন করে যিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন যার মধ্যে কিছু একবার ওয়াকফ বোর্ডের কাছে ন্যস্ত ছিল। নতুন আইনটি সমস্ত নিবন্ধিত ওয়াকফকে ওয়াকফ এবং ওয়াকফের জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির বিবরণ ফাইল করার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে।
সংশোধনীতে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করে সরকারি জমির অপব্যবহার বন্ধ করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে সংশোধনীর আগে বা পরে ওয়াকফ হিসাবে ‘শনাক্ত’ বা ‘ঘোষিত’ কোনও সরকারি সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না। বিরোধের ক্ষেত্রে, কালেক্টর তদন্ত পরিচালনা করবেন।
বর্তমান আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত-কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, যা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সংশোধনী এটিকে পরিবর্তন করে বলে যে ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের পর থেকে দুই বছরের মধ্যে একটি মামলা গঠন করা যেতে পারে।
ওয়াকফ অ্যাক্টের ধারা ৪০, যা বোর্ডকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে এমন কোনও সম্পত্তি সম্পর্কিত সংগ্রহের অনুমতি দেয়, বিলুপ্ত করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে দুইজন মহিলা সদস্য ছাড়াও ওয়াকফ বোর্ডে দু’জন অমুসলিম সদস্য নিয়োগ করা হবে।
একটি ওয়াকফ দলিল সম্পাদন ছাড়া ওয়াকফ তৈরি বন্ধ করা হয়েছে, এবং কালেক্টর আবেদনের সত্যতা সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করবেন। যদি এটি বিতর্কিত বা সরকারি সম্পত্তি পাওয়া যায়, তবে নিবন্ধন করা হবে না।
ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এ প্রস্তাবিত সংশোধনী শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়, বরং ভারতের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আইনি অধিকারের উপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে।
ওয়াকফ সম্পত্তির স্বায়ত্তশাসনকে অপসারণ, বৈষম্যমূলক ও ইচ্ছামতো শর্ত চাপিয়ে এবং নজিরবিহীন সরকারি অতিসক্রিয়তার পথ প্রশস্ত করার মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলি সংবিধানের ১৪, ২৫, ২৬ ও ৩০০এ ধারাকে লঙ্ঘন করছে। এই বিল নিষ্পত্তি হওয়া ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইনি নীতি ও বিচার বিভাগীয় রায়কে অমর্যাদা করছে। ১৯৫৪ সালের শিরুর মুট মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং ২০১০ সালের ভারত সরকার বনাম আর গান্ধি মামলায় বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন ট্রাইবুনালের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে যাতে ধর্মীয় বিষয়ে স্ব-শাসিত হয়। এই বিল সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও অমর্যাদা করছে। ওয়াকফ সম্পত্তির প্রধান রক্ষাকবচগুলির অপসারণ ১৯৯৭ সালের এল চন্দ্র কুমার বনাম ভারত সরকারের মামলায় প্রতিষ্ঠিত নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। এই মামলায় বলা হয়েছিল, ধর্মীয় তহবিলের বিচার বিভাগীয় মূল্যায়নের প্রয়োজন ও এই সম্পত্তিকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করা দরকার।
তাছাড়া, সকল ধর্মের ধর্মীয় দান-তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই সংশোধনী এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করছে। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বিন্যাসকে ঘেটেঁ দিচ্ছে এবং ভারতের আত্মপরিচয়ের মূল ভাবনা অর্থাৎ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে খর্ব করছে। এই সব সাংবিধানিক লঙ্ঘন, আইনি পরস্পর বিরোধিতা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনার নিরিখে প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল করা একান্ত অপরিহার্য। ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের সংরক্ষণ, ওয়াকফ সম্পত্তির সুরক্ষা ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ইত্যাদি দাবি করছে, সংসদের বিবেচনার মাধ্যমে এই বিল প্রত্যাহার করা হোক।
লেখকঃ ওবাইদুর রহমান বুখারী
(লেখাটি যুবপ্রত্যাশার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল)