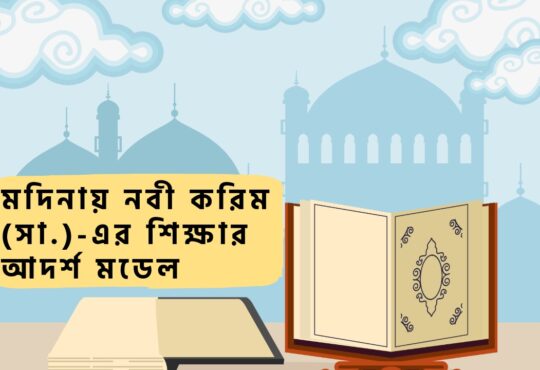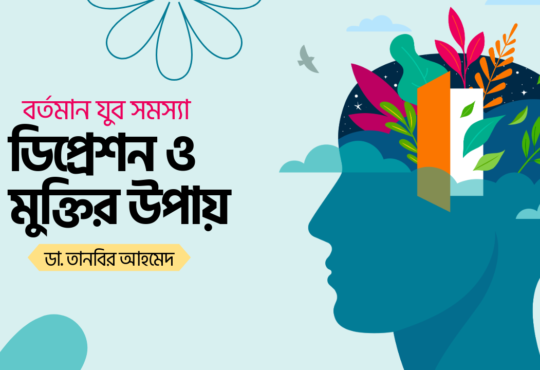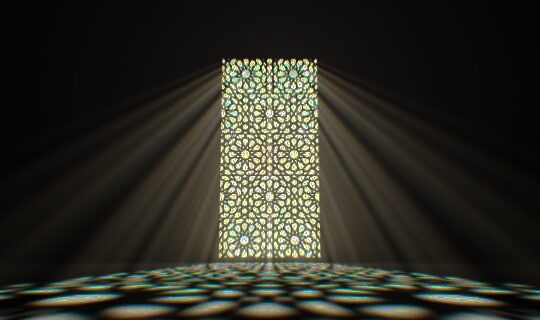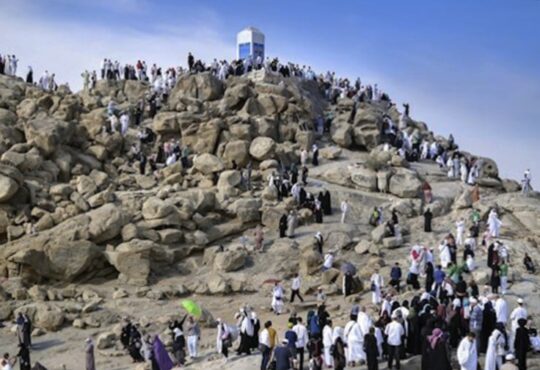জীবনের শক্তি
মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী। তবে ক্ষণস্থায়ী মানে এই নয় যে তা অক্ষম বা মূল্যহীন। বরং জীবনের এই অস্থায়িত্বই তাকে করে তোলে বিস্ময়কর। একে বলা যায় এক ধরনের ‘অসম্পূর্ণতার ভেতর নিখুঁততা’। ভৌত অর্থে জীবন হলো এক চলমান প্রক্রিয়া। আমাদের চারপাশের সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বস্তুগত উদ্ভাবন আসলে জীবনের অসাধারণত্বকেই প্রতিফলিত করে। অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ তার সাধনার শিখরে পৌঁছতে পারে, নিজের নির্ধারিত সাফল্যের সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে উঠতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, জীবন আসলে ভরপুর শক্তি, গতি ও সম্ভাবনায়।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়: সব মানুষ কি একইরকম জীবনযাপন করে? এর উত্তর অবশ্যই না।
কারণ “জীবনের প্রক্রিয়া” সবার জন্য এক নয়। একে আমরা জলের উপমায় ব্যাখ্যা করতে পারি। জল আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত বস্তু। একদিকে পাহাড়ি ঝরনার বয়ে চলা জলের স্বভাব অন্যদিকে স্থির পুকুরের জলের স্বভাবের থেকে একেবারেই আলাদা। ঝরনার জল তার স্বচ্ছতা ধরে রাখতে পারে কারণ এর ভেতরে আছে গতি, সহনশীলতা, শিলার সঙ্গে সংঘর্ষের সাহস এবং উচ্চতা থেকে পতনের শক্তি। বিপরীতে, স্থির পুকুরের জল কোনো গতি না থাকার কারণে ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং শেষে দূষিত হয়ে যায়।
জলের উপমা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝায় যে স্থবিরতা অর্থাৎ প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার সাহসের অভাব হলো বিশুদ্ধতা হারানো, অর্থাৎ সাফল্যের মৃত্যুর নামান্তর। অন্যভাবে বললে, জীবনে অসাধারণ অর্জন সম্ভব নয় যদি কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ না হয়। এই শর্তগুলো কখনও কঠিন, জটিল, আবার কখনও ক্লান্তিকরও হতে পারে।
কিন্তু সমস্ত শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আচরণ, সময় ও সক্ষমতার মধ্যে ‘সমতার ত্রিভুজ’ বজায় রাখা, যাকে বলা যায় সাফল্যের ত্রিভুজ সমীকরণ। এই সমতার ত্রিভুজে তিনটি বাহু – আচরণ, সময় এবং সক্ষমতা পরস্পর নির্ভরশীল এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই সমতা রক্ষা হয়, তখন মানুষ পরিস্থিতির চাপ অনুযায়ী নিজের আচরণকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারে, প্রয়োজনে তা সংস্কার বা পরিবর্তন করতে পারে, আর সেই সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমেই নিজের লুকায়িত সক্ষমতাকে বাস্তব সাফল্যে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যারা অতীতে এই ‘ত্রিভুজী ভারসাম্য’ অর্জন করেছিল, তারা আজও বেঁচে আছেন এবং ভবিষ্যতেও স্মরণীয় থাকবেন। এরা জন্মগতভাবে প্রতিভাবান না হলেও হয়ে উঠেছেন ‘ইতিহাস-নির্মাতা’, ‘ধারা-প্রবর্তক’ ও ‘প্রভাবশালী’ ব্যক্তিত্ব। সংক্ষেপে, তারা অন্যদের জন্য দিশারী হয়ে উঠেছেন।
“ত্রিভুজী ভারসাম্য” ও মানব-প্রকৃতি
‘ত্রিভুজী ভারসাম্য’-এর তিনটি বাহু হলো আচরণ, সময় ও সম্ভাবনা। আচরণ বোঝায় কর্মের বহিঃপ্রকাশ। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কোনো কাজ বাস্তবায়নের আগে মানুষের মনের মধ্যে তা গঠিত হয়। এই মানসিক স্তরের ধারণাই হলো কর্মের অভ্যন্তরীণতা। যখন কোনো কাজ বারবার মানসিক স্তর থেকে কর্মতৎপরতার স্তরে রূপান্তরিত হয়, তখন তা আচরণের অংশে পরিণত হয়।
সময়কে বোঝাতে হয় এর পরিমাণগত ও গুণগত দুই দিক দিয়েই। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরের শীতে মাঠে কোনো কৃষিকাজ হয় না। এখন যদি কেউ প্রবল কর্মইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা বরফ ও তুষার সরিয়ে জমিতে বীজ বপন করে, তাহলে কি সে ফসল পাবে? না। কারণ, গুণগত দিক থেকে এটি উপযুক্ত সময় নয়। অর্থাৎ, কার্যকর ফলাফলের জন্য সময়ের দুই মাত্রাকে একত্রিত হতে হয়।
‘সম্ভাবনা’ হলো মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা, অনাবিষ্কৃত জৈবশক্তির ভাণ্ডার। ভৌত বিজ্ঞানে এটি বাঁধে জমা পানির স্থিতিশক্তির মতো। একবার পানি নেমে এলে সেই শক্তি রূপান্তরিত হয় গতিশক্তি-তে। দর্শনের ভাষায়, বীজ হলো সম্ভাব্য বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হলো বাস্তবায়িত বীজ।
এই তিন উপাদানের ইতিবাচক সমীকরণ একটি সুসংগঠিত ও ফলমুখী কর্ম জন্ম দেয়। এমন একটি কর্ম যা রূপান্তরমূলক অর্থাৎ, যা নিম্ন স্তরকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে। তবে সব মানুষই আজীবন এই ‘ত্রিভুজী ভারসাম্য’ বজায় রাখতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন অসাধারণ ধারাবাহিকতা, সাহস, ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প। কেননা মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই দুর্বল; ফলে মানুষ সর্বদা পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে স্বীকার করেই ইসলাম প্রবর্তন করেছে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি।
এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার নাম হলো আত্মসংযম অর্থাৎ, আত্ম-প্রভুত্ব থেকে আত্ম-শৃঙ্খলায় রূপান্তরমূলক যাত্রা। আধুনিক জীবনের যান্ত্রিক কাঠামো আমাদের এমনভাবে শর্তায়িত করেছে যে আমরা বিশ্বাস করি আত্ম-প্রভুত্বই সাফল্য অর্জনের একমাত্র দ্রুত উপায়। অথচ, বাস্তবে আমরা প্রায়ই ব্যর্থ হই কিংবা অর্জিত সাফল্য প্রত্যাশা অনুযায়ী হয় না। একবার যখন আমরা তা উপলব্ধি করি, তখনই আত্ম-প্রভুত্ব-এর মনস্তত্ত্ব ভেঙে দিয়ে আত্মসংযম-এর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি।
এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মার্কিন সমাজমনোবিজ্ঞানী রয়ের বাউমাইস্টার তাঁর “এগো ডিপ্লেশন” তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, “ব্যক্তিগত সাফল্যের ক্ষেত্রে আত্মসংযম অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সমর্থিত একটি কারণ।” তিনি আরও স্বীকার করেন যে, “আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতাই আমাদের সময়ের প্রধান সামাজিক রোগ।”
মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বলছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যাস ভাঙা, বিলম্বিত তৃপ্তি এবং কর্মসম্পাদন নিয়ন্ত্রণ এসবই সরাসরি নির্ভরশীল যে ধরনের আত্মসংযম প্রয়োগ করা হয় তার ওপর। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, আত্মসংযমের একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো “পুরস্কার ও শাস্তি পদ্ধতি”।
ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পুরস্কার ও শাস্তি
মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই অবস্থাগুলিই আসলে বাহ্যিক উদ্দীপনা বা বলা যায় ‘জীবনযাত্রার পরিবেশ’ নির্ধারণ করে, যা শুধু কর্ম-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না বরং মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ‘জ্ঞাত আচরণ’-কেও পরিবর্তিত করে। উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কই মানুষের ‘আচরণগত ধারা’ বা ব্যক্তিত্বের কার্যধারাকে গঠন করে।
এখান থেকে বোঝা যায়, যদি ‘জীবনযাত্রার পরিবেশ’ এমনভাবে অনুকূল হয় যে আচরণ, সময় ও সামর্থ্যকে ‘ত্রিভুজী ভারসাম্যে’ রাখা সম্ভব হয়, তবে জীবন হয়ে ওঠে ফলপ্রসূ ও কার্যকর; অর্থাৎ অর্থপূর্ণ জীবন। অন্যদিকে, যদি এই ‘ত্রিভুজী ভারসাম্য’ অর্জিত না হয়, তবে জীবন হয়ে ওঠে অনুৎপাদনশীল; অর্থাৎ অর্থহীন জীবন। সুতরাং, বলা যায় যে ‘জীবনযাত্রার পরিবেশ’ যদি নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিবর্তিত হয়, তবে আচরণেও সমান মাত্রায় পরিবর্তন আসবে। এটাই মানব আচরণের স্বাভাবিক প্রবণতা। এখন এই প্রেক্ষাপটে আমরা পুরস্কার ও শাস্তি পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করতে পারি।
যুক্তি দিয়ে বলা যায়, ইসলাম পুরস্কার ও শাস্তিকে এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে সুপারিশ করে যার মাধ্যমে ‘জীবনযাত্রার পরিবেশ’কে পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় মাত্রায় আচরণের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়।
এখানে স্পষ্ট করে বলা জরুরি যে, ইসলামের পুরস্কার ও শাস্তি মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক-আধ্যাত্মিক পদ্ধতি। এটি মনের, আত্মার এবং বস্তুর মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে। বস্তু দ্বারা বোঝানো হয় ‘জীবন-পরিস্থিতি’, যার মধ্যে রয়েছে, মালেক বিননাবির ভাষায়, সময় ও মাটির সামাজিক অর্থ। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তি-স্তরে তার ‘জীবন-পরিস্থিতি’ পরিবর্তন করতে সক্ষম, যদি সে মন, আত্মা ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে চিনতে পারে। পুরস্কার ও শাস্তি এই দুইটি মাধ্যম মানুষকে এই সম্পর্ক চিনতে এবং পুনঃসংযুক্ত হতে সহায়তা করে।
যুক্তি দিয়ে বলা যায়, পুরস্কারের অনুভূতি কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে করার জন্য; অর্থাৎ মন ও আত্মা বস্তুজগতে পছন্দনীয় পথে কার্যকর হতে অনুপ্রাণিত হয়। বিপরীতে, শাস্তির অনুভূতি কর্মশক্তিকে সতর্ক করে না করার জন্য; অর্থাৎ মন ও আত্মাকে সাবধান করে দেয় যেন তারা বস্তুজগতে অপছন্দনীয় পথে কার্যকর না হয়। নৈতিক ভাষায় বললে, পুরস্কার কর্মকে নৈতিকভাবে সঠিকের দিকে ঠেলে দেয় আর শাস্তি কর্মকে নৈতিকভাবে ভুলের দিক থেকে বিরত রাখে। একইভাবে, আইনগত প্রেক্ষাপটে পুরস্কার আইনসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত সামাজিক আচরণকে উৎসাহিত করে, আর শাস্তি আইনবিরুদ্ধ ও অন্যায় সামাজিক আচরণকে অপরাধে পরিণত করে।
পুরস্কার ও শাস্তির প্রকৃতি
ইসলামে পুরস্কার ও শাস্তির গতিশীলতাকে বোঝার জন্য এর উচ্চতর উদ্দেশ্যসমূহ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এখানে আমি দুটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করব।
প্রথম উচ্চতর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কর্তৃত্বের কেন্দ্রীয়তা প্রতিষ্ঠা করা। এর অর্থ হলো এই সচেতনতা রাখা যে কেবল আল্লাহই এমন একমাত্র সত্তা যিনি নির্দিষ্ট আচরণকে পরিত্যাগ বা সম্পাদনের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ, কোনো আচরণের পুনঃপুন পরিত্যাগ বা পুনরাবৃত্তি মনস্তাত্ত্বিক অর্থে এমনভাবে অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত নয় যাতে তার অন্তর্নিহিত অর্থ হারিয়ে যায়।
কুরআন মানুষকে উচ্চতর মানসিক-আধ্যাত্মিক আচরণের অভিজ্ঞতা অর্জনে উৎসাহিত করে। সেই প্রেক্ষিতে, পুনরাবৃত্তি কেবল কাজের অনুকরণ নয়। বরং এর মধ্যে নিহিত থাকে এক ধরনের নতুনভাবে সতেজকরণ বা, আমি যাকে বলি অভ্যাসমুক্তকরণ। সচেতন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আচরণের অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্যের উচ্চতর স্তরকে উপলব্ধি করা।
বেশিরভাগ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে যেমন বি.এফ. স্কিনারের বিখ্যাত “অপারেন্ট কন্ডিশনিং” তত্ত্বে আল্লাহর কর্তৃত্বকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে ধরা হয় না। অন্য দিক থেকে বললে, যদি কোনো আচরণ কেবল অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তবে তার অর্থ ও উদ্দেশ্য দুটোই হারিয়ে যায়। ফলে অভ্যাসীকরণ শেষ পর্যন্ত আচরণকে কেবল শারীরিক কার্যসম্পাদনায় সীমাবদ্ধ করে ফেলে। ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যকলাপকে সুশৃঙ্খল করা। ইসলামে পুরস্কার ও শাস্তির ধারণার মাধ্যমে মানবজীবনে শান্তি ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
একদিকে ইসলাম অন্যায়, দুষ্টুমি, ভণ্ডামি, জুলুম ও অসহিষ্ণুতার মতো আচরণের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। অন্যদিকে, ইসলাম ন্যায়পরায়ণ, শান্তিপ্রিয়, সৎ, সত্যবাদী ও সহিষ্ণু আচরণের জন্য অফুরন্ত পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছে। এসব আচরণ কেবল মানুষের আত্মিক জীবনে নয়, বরং পারস্পরিক সম্পর্কেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।
কুরআনের বর্ণনায়, চিরস্থায়ী পুরস্কার হলো জান্নাত, যা চিরস্থায়ী শান্তি, দয়া ও অফুরন্ত নিয়ামতের আবাস। আর চিরস্থায়ী শাস্তি হলো জাহান্নাম, যা চিরস্থায়ী কষ্ট, যন্ত্রণা ও শাস্তির আবাস। কুরআনিক পরিভাষায়, জান্নাত হলো ঈমানের বীজ থেকে উৎপন্ন সৎকর্ম বা হাসানাত এর পুরস্কার। অপরদিকে, জাহান্নাম হলো কুফরের বীজ থেকে উৎপন্ন কু-কর্ম বা সাইয়্যিআত এর শাস্তি। উপমা দিয়ে বললে, যেমন একটি বীজের গুণ তার কান্ড, ডাল, পাতা ও ফলের গুণ নির্ধারণ করে, তেমনই ঈমানের বীজের গুণ পুরস্কারের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। একইভাবে, কুফরের বীজের গুণ শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণ করবে।
চিরস্থায়ী পুরস্কার ও শাস্তির প্রসঙ্গে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যেন তারা সাইয়্যিআত আচরণকে হাসানাতে রূপান্তরিত করে চিরন্তন শান্তির ভালোবাসা আর চিরস্থায়ী শাস্তির ভয়ের মাধ্যমে। কিছু মুসলিম ভুলভাবে ইসলামের পুরস্কার-ধারণাকে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ওয়াল্টার মিশেলের বিখ্যাত মার্শমেলো এক্সপেরিমেন্টে উত্থাপিত “ডিলেইড গ্র্যাটিফিকেশন” ধারণার সঙ্গে তুলনা করেন। যদিও এক অর্থে স্বীকার করা যায় যে জান্নাত হলো তাৎক্ষণিক পশুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি ও কামনার নিয়ন্ত্রণের পুরস্কার, তবুও এর মানে এই নয় যে মার্শমেলো তত্ত্ব ইসলামে ‘পুরস্কার-প্রণোদিত’ আচরণের দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মার্শমেলো তত্ত্বে যেহেতু কোনো নৈতিক কর্তৃত্ব নেই, তাই সেখানে কোনো কিছু কাকে সামনে রেখে বিলম্বিত করা হচ্ছে, আর সেটি নৈতিকভাবে সঠিক কি না, সে ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা থাকে না।
লিখেছেন: মালিক গাজি